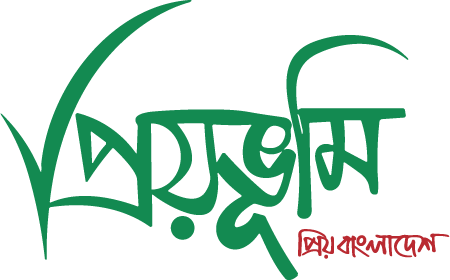
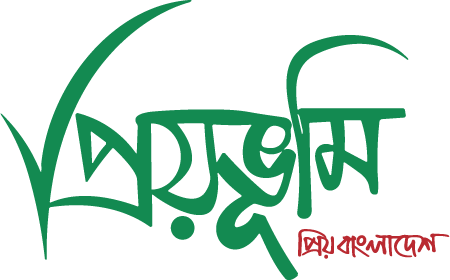

১৯৭১ সালের ৩১ জুলাই রাতে সংঘটিত কামালপুরের যুদ্ধ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং তীব্রতম যুদ্ধ হিসেবে স্মরণীয়। এটি ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রথম আনুষ্ঠানিক বা কনভেনশনাল যুদ্ধ, যা মুক্তিবাহিনীর গেরিলা কৌশল থেকে সরাসরি ও সংগঠিত আক্রমণের দিকে অগ্রসর হওয়ার একটি ট্রানজিশন মুহূর্তকে চিহ্নিত করে। জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলার ধানুয়া কামালপুর ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী গ্রাম কামালপুরে অবস্থিত এই যুদ্ধ চার মাসেরও বেশি সময় ধরে চলেছিল, যার মধ্যে একাধিক খণ্ডযুদ্ধ এবং চারটি সেট পিস যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই প্রতিবেদনটি মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমদের ‘রক্তে ভেজা একাত্তর’, অন্যান্য ঐতিহাসিক সূত্র এবং সমসাময়িক প্রতিবেদন থেকে সংগৃহীত তথ্যের সমন্বয়ে এই ঐতিহাসিক রাতের ঘটনা, কৌশল এবং মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের একটি বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করে।
কামালপুরের কৌশলগত গুরুত্ব
মেঘালয়ের সীমান্তের কাছে অবস্থিত ধানুয়া কামালপুর ইউনিয়নের কামালপুর ছিল কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ভৌগোলিক অবস্থান মুক্তিবাহিনীর অনুপ্রবেশ ঠেকাতে পাকিস্তানি বাহিনীর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা পয়েন্ট হিসেবে কাজ করত। কামালপুর দখল করতে পারলে মুক্তিবাহিনী ঢাকার দিকে অগ্রসর হতে পারত, যেখানে ব্রহ্মপুত্র নদ ছাড়া আর কোনো উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক বাধা ছিল না। এই সম্ভাব্য হুমকি মোকাবিলায় পাকিস্তানি বাহিনী ৬ জুন, ১৯৭১-এর মধ্যে কামালপুর সীমান্ত ঘাঁটিতে (বিওপি) ৩১ বেলুচ রেজিমেন্টের দুটি প্লাটুন এবং একটি রাজাকার প্লাটুন মোতায়েন করে। এই ঘাঁটিতে আটটি বাঙ্কার, স্থল মাইন, কাঁটাতারের বেড়া, বুবি ট্র্যাপ এবং বাঁশের কঞ্চি সমন্বিত একটি দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়।
যুদ্ধের প্রস্তুতি
কামালপুরের গুরুত্ব উপলব্ধি করে মুক্তিবাহিনী এই ঘাঁটি দখলের জন্য একটি সমন্বিত আক্রমণের পরিকল্পনা করে। এর আগে, ১২ জুন নায়েব সুবেদার সিরাজের নেতৃত্বে ১৫০ জন ইপিআর সৈন্য এই ঘাঁটিতে আক্রমণ চালায়, কিন্তু এতে পাকিস্তানি বাহিনীর তেমন ক্ষতি হয়নি। জুলাই মাসে প্রথম, তৃতীয় এবং অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সমন্বয়ে জেড ফোর্স গঠিত হলে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনের দায়িত্ব তিনটি ব্যাটালিয়নের উপর অর্পিত হয়। প্রথম ইস্ট বেঙ্গলকে কামালপুর বিওপি দখলের নির্দেশ দেওয়া হয়।
অপারেশনের নেতৃত্বের জন্য চারটি কোম্পানির দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়--
আলফা কোম্পানি, ক্যাপ্টেন মাহবুবুর রহমানের নেতৃত্বে, উঠানিপাড়ায় রোডব্লক তৈরির দায়িত্ব পায়।
ব্রাভো কোম্পানি, ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে।
চার্লি কোম্পানি, লেফটেন্যান্ট মোহাম্মদ মান্নানের নেতৃত্বে।
ডেল্টা কোম্পানি, ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন মমতাজের নেতৃত্বে।
যুদ্ধের তদারকি করেন ব্যাটালিয়ন কমান্ডার মেজর মঈনুল হোসেন চৌধুরী এবং জেড ফোর্স কমান্ডার মেজর জিয়াউর রহমান।
২৮ জুলাই বিকেলে ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে একটি দল ছদ্মবেশে রেকি (টহল) পরিচালনা করে। একই রাতে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিনের নেতৃত্বে আরেকটি দল রেকির জন্য বের হয়, কিন্তু পাকিস্তানি লিসনিং পোস্টের কাছে পৌঁছলে দুই পাকিস্তানি সৈন্য তাদের উপস্থিতি টের পায়। মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে দুই হানাদার সৈন্য নিহত হয়। এ ঘটনায় পাকিস্তানি বাহিনী ধরে নেয় যে এটি ভারতীয়দের চোরাগুপ্তা হামলা। ফলে জেনারেল নিয়াজীর নির্দেশে ঢাকা থেকে অতিরিক্ত সৈন্য এবং অস্ত্র-গোলাবারুদ কামালপুরে পাঠানো হয়।
যুদ্ধের শুরু: ৩১ জুলাই ১৯৭১
দুই দফা রেকির পর ৩১ জুলাই রাত সাড়ে তিনটায় আক্রমণের সময় চূড়ান্ত করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ব্রাভো এবং ডেল্টা কোম্পানি সরাসরি আক্রমণ করবে, আলফা কোম্পানি উঠানিপাড়ায় কাট-অফ পার্টি হিসেবে রোডব্লক তৈরি করবে, এবং চার্লি কোম্পানি ফর্মিং-আপ-প্লেসে (এফইউপি) গাইড করবে। ভারতীয় বাহিনী আর্টিলারি সহায়তা প্রদান করবে।
৩০ জুলাই সূর্যাস্তের পর তুমুল বৃষ্টির মধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা ভারতের মহেন্দ্রগঞ্জে পৌঁছান। চেকআপ শেষে ভারতীয় আর্টিলারির সঙ্গে সমন্বয়ের পর তারা কামালপুরের উদ্দেশে রওনা হন। তবে বৃষ্টির কারণে চলাচলে বিলম্ব হওয়ায় এফইউপিতে পৌঁছাতে দেরি হয়।
ভুল বোঝাবুঝি ও আক্রমণের শুরু
পরিকল্পনা ছিল, ক্যাপ্টেন হাফিজ এফইউপিতে পৌঁছে সংকেত দেওয়ার পর ভারতীয় মাউন্টেন ব্যাটারি আর্টিলারি ফায়ার শুরু করবে। কিন্তু ভুল বোঝাবুঝির কারণে রাত সাড়ে তিনটায় মুক্তিযোদ্ধারা এফইউপিতে পৌঁছানোর আগেই আর্টিলারি ফায়ার শুরু হয়। এতে পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান টের পেয়ে পাল্টা আর্টিলারি ফায়ার শুরু করে। ফলে সদ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।
পাকিস্তানি বাহিনীর দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ভারতীয় আর্টিলারি ফায়ার কোনো কাজে না আসায় ব্রাভো এবং ডেল্টা কোম্পানির জন্য আক্রমণ কঠিন হয়ে পড়ে। তবুও ব্রাভো কোম্পানি শত্রু বাঙ্কারের দিকে এগিয়ে যায়। এ সময় মাইন ফিল্ডে পড়ে নায়েব সুবেদার সিরাজের একটি পা বিস্ফোরণে উড়ে যায়। একটি শেলের টুকরো ক্যাপ্টেন হাফিজের হাতের চাইনিজ স্টেনের বাঁট উড়িয়ে দেয়। কামান ও মর্টারের গোলায় চারদিক আতশবাজির মতো আলোকিত হয়, এবং হতাহতদের আর্তচিৎকার যুদ্ধক্ষেত্রকে আরও ভয়াবহ করে তোলে।
হঠাৎ ওয়্যারলেস বিকল হয়ে যাওয়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। ভারতীয় আর্টিলারি ফায়ারও সংকেতের অভাবে থামেনি। দুই পক্ষের তীব্র গোলাগুলির মধ্যে চিৎকারের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষাও কঠিন হয়ে পড়ে। এ সময় ব্রাভো কোম্পানির টুআইসি সুবেদার খায়রুল বাশার হাফিজকে জানান, অনেক সৈন্য হতাহত হয়েছে, এবং ডেল্টা কোম্পানির কমান্ডার ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন মমতাজ শহীদ হয়েছেন।
ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন মমতাজের বীরত্ব
এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন মমতাজ অসাধারণ নেতৃত্ব প্রদর্শন করেন। শত্রুদের বিভ্রান্ত করতে তিনি উর্দুতে চিৎকার করে বলেন, “সবাই এখনই সারেন্ডার কর, নয়তো একজনকেও জীবিত ছাড়ব না।” একই সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করতে বলেন, “ইয়াহিয়া খান এখনও এমন বুলেট তৈরি করতে পারেনি, যা মমতাজকে ভেদ করবে। যদি মরতেই হয়, তবে এক পাকিস্তানি সেনাকে সঙ্গে নিয়ে বাংলার মাটিতে শহীদ হও।”
তার অনুপ্রেরণায় ডেল্টা কোম্পানির ২০-২৫ জন মুক্তিযোদ্ধা দুর্ধর্ষভাবে প্রথম ডিফেন্স কর্ডনের শেল-প্রুফ বাঙ্কারে প্রবেশ করে। তখন সালাউদ্দিন দেখেন, পাকিস্তানি সেনারা দ্বিতীয় লাইনে ফিরতি আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি মেগাফোনে সুবেদার হাইকে ডানদিকে যাওয়ার নির্দেশ দেন, কিন্তু শব্দের কারণে সুবেদার হাই তা শুনতে পাননি। তার প্লাটুনের ৪০ জনের মধ্যে তখন মাত্র ১৫ জন জীবিত ছিলেন।
সালাউদ্দিনের বিপজ্জনকভাবে এগিয়ে যাওয়া দেখে সুবেদার হাই তাকে পিছু হটতে বলেন, কিন্তু তিনি তা অগ্রাহ্য করেন। তিনি সহযোদ্ধাদের বলেন, “খোদার কসম, তোরা কেউ পিছু হটবি না। মরতে হয় তো পাকিস্তানিদের মেরে মর, বাংলাদেশের মাটিতে মর।” এরপর পাকিস্তানি গুলি ও গোলার আঘাতে তিনি শহীদ হন। তার মরদেহ উদ্ধার করতে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হায়াত আলী এবং সিরাজও শহীদ হন।
আহত কমান্ডার ও নেতৃত্বহীনতা
মর্টার শেলের স্প্রিন্টারের আঘাতে ব্রাভো কোম্পানির কমান্ডার ক্যাপ্টেন হাফিজ এবং চার্লি কোম্পানির কমান্ডার লেফটেন্যান্ট মান্নান আহত হন। ফলে তিনটি কোম্পানিই নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে। তবুও মুক্তিযোদ্ধারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পাকিস্তানি বাঙ্কারে আক্রমণ চালিয়ে যান। কিন্তু হানাদারদের অবিরাম গোলাগুলিতে হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মেজর মঈনুল হোসেন চৌধুরী পিছু হটার সিদ্ধান্ত নেন।
কাট-অফ পার্টির সাফল্য
আলফা কোম্পানি, ক্যাপ্টেন মাহবুবুর রহমানের নেতৃত্বে, উঠানিপাড়ায় অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মাইন স্থাপন করে রোডব্লক তৈরি করে। রাত সাড়ে চারটায় বকশীগঞ্জ থেকে আসা দুটি ট্রাক পাকিস্তানি সেনা মাইন বিস্ফোরণে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অতর্কিত হামলায় পড়ে। এতে ১০ জন হানাদার সেনা এবং একজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।
যুদ্ধের ফলাফল
কামালপুরের প্রথম যুদ্ধে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন মমতাজসহ ৩১ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন, এবং ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিনসহ ৬৫-৬৬ জন আহত হন। পাকিস্তানি বাহিনীর প্রায় ৫০-৫৯ জন সেনা নিহত এবং ৬০ জন আহত হয়। যদিও মুক্তিবাহিনী কামালপুর বিওপি দখল করতে পারেনি, তবুও এই যুদ্ধে তারা অসীম সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনীকে সম্মুখ সমরে দাঁতভাঙা জবাব দিতে প্রস্তুত থাকার বার্তা দেয়।
মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমদ তার বই *রক্তে ভেজা একাত্তর*-এ লিখেছেন: “সামান্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অনভিজ্ঞ গ্রামীণ যুবকরা কামানের সাহায্য ছাড়াই মাইন ফিল্ড, কাঁটাতার ডিঙিয়ে প্রমত্ত ঢেউয়ের মতো এগিয়ে কীভাবে এই সুরক্ষিত ঘাঁটির কিছু অংশ দখল করেছিল। সে কথা ভেবে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ি। একমাত্র গভীর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ দৃঢ় মনোবলের অধিকারী, মৃত্যুঞ্জয়ী সুইসাইড স্কোয়াডের পক্ষেই এমনি আক্রমণে অংশগ্রহণ সম্ভব, যাদের কাছে জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।”
অন্যান্য সমসাময়িক ঘটনা
৩১ জুলাই, ১৯৭১-এ কামালপুর ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ফ্রন্টে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ১১ নম্বর সেক্টরের অধীনে লেফটেন্যান্ট এস আই নুরুন্নবী খানের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী জামালপুরের ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে বাহাদুরাবাদ ঘাটে পাকিস্তানি সেনা অবস্থানে অতর্কিত হামলা চালায়। এক ঘণ্টার তুমুল যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর গোলাবারুদ ভর্তি একটি বার্জ ডুবে যায় এবং বেশ কয়েকজন সেনা হতাহত হয়।
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি ঘাঁটিতে আক্রমণ চালিয়ে কয়েকটি বাঙ্কার ধ্বংস করে এবং বেশ কয়েকজন সেনাকে হতাহত করে। আক্রমণের চাপে পাকিস্তানি সেনারা পিছু হটে। কুমিল্লায় চৌদ্দগ্রাম এবং জগন্নাথ দীঘি থেকে আসা পাকিস্তানি সেনাদের উপর মুক্তিযোদ্ধারা অতর্কিত আক্রমণ চালায়, যাতে হানাদাররা হতাহত হয়।
এদিকে, ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি কূটনীতিক আবুল মাল আবদুল মুহিত পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। তিনি এনবিসি টেলিভিশনকে বলেন, “একটি আত্মহননকারী সরকারের সঙ্গে যুক্ত থাকা অসম্ভব।”
ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দিল্লিতে বলেন, বাংলাদেশের সমস্যা মোকাবিলায় বিরোধী দলগুলো প্রাথমিকভাবে তার হাত শক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিলেও কিছু দল এখন বাধা সৃষ্টি করছে। তিনি শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়ে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করেন।
ভারতের কংগ্রেস দলীয় সদস্য প্রণব মুখার্জি রাজ্যসভায় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। নেপালের জাতীয় পঞ্চায়েতের কয়েকজন সদস্য বাংলাদেশে গণহত্যার বিষয়ে তাদের সরকারের ঔদাসীন্যে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য নেপালের ভূমিকার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।
পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষ ঢাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে এবং গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের উপর নজরদারি বাড়ায়। এছাড়া, আবদুল জব্বার, কবরীসহ ১৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তলব করা হয়।
কামালপুরের প্রথম যুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি অমর কাহিনী। এটি শুধু মুক্তিবাহিনীর প্রথম আনুষ্ঠানিক যুদ্ধই নয়, বরং তাদের অসীম সাহস, দৃঢ়তা এবং দেশপ্রেমের প্রতীক। ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন মমতাজ, ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিন আহমদ, এবং অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ এই যুদ্ধকে একটি ঐতিহাসিক মর্যাদা দিয়েছে। যদিও বিওপি দখল সম্ভব হয়নি, তবুও এই যুদ্ধ পাকিস্তানি বাহিনীকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে মুক্তিবাহিনী শুধু গেরিলা যুদ্ধ নয়, সম্মুখ সমরেও শক্তিশালী প্রতিপক্ষ।
তথ্যসূত্র:
রক্তে ভেজা একাত্তর – মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ (বীর বিক্রম)
কামালপুর ১৯৭১ – সম্পাদক মুহাম্মদ লুৎফল হক
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: দশম খণ্ড
বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ: সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস, সেক্টর দুই ও এগারো
ইত্তেফাক, ১ ও ২ আগস্ট ১৯৭১
আনন্দবাজার পত্রিকা ও যুগান্তর, ভারত, ১ ও ২ আগস্ট ১৯৭১
মন্তব্য করুন